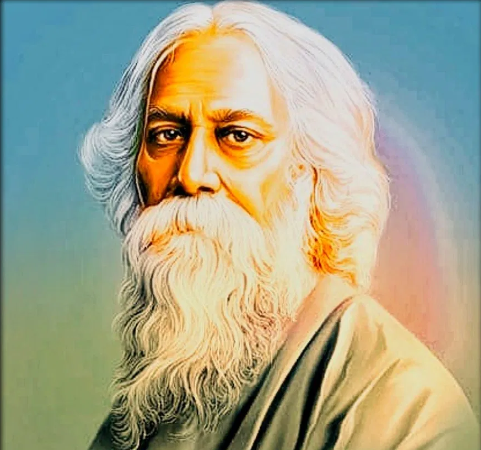আলোয় ভুবন ভরাI

ডক্টর রাজকুমার রায় চৌধুরী
আমরা যদি ফিরে যাই মানব সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং কল্পনা করি– আমাদের কোনো পূর্বপুরুষ আফ্রিকার কোনো এক বিস্তৃৃত ঘাসের শয্যায় শুয়ে আছে। সূর্য অস্ত যাবার অনেকক্ষণ পর, আকাশ যদি মেঘমুক্ত থাকে, তাহলে সে দেখবে রাতের আকাশে হাজার হাজার উজ্জ্বল তারা৷ ঠিক যেন অসংখ্য আলোর বিন্দু আকাশে ঝুলে আছে৷ হীরে তখনো মানুষ আবিষ্কার করেনি, না হলে মনে হত অজস্র হীরের টুকরো কেউ আকাশের গায়ে সেঁটে দিয়েছে৷ বহুদূর থেকে এই তারাগুলি থেকে আসা আলোই তার চোখে তারাগুলিকে প্রতীয়মান করে তুলেছে৷ তখনো সে জানেনা, দিনের বেলা, প্রায় জ্বলন্ত-আগুনের-গোলার মত দেখতে সূর্যও– একটি তারা৷ কিন্তু অন্যান্য তারার তুলনায় সূর্য পৃথিবীর খুব কাছে থাকার জন্য তার আলো এত প্রখর যে, অস্ত বা উদয়ের সময় ছাড়া সূর্যের দিকে তাকালে, চোখ ঝলসে যাবে৷
রাতের চাঁদের আলো অতি স্নিগ্ধ৷ তখন মানুষ জানতো না যে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই৷ আমাদের চোখে চাঁদের যে-আলো ধরা দেয় তা প্রতিফলিত আলো৷
শুধু মানুষ কেন, দৃষ্টিহীন প্রাণী ছাড়া, পৃথিবী সমস্ত প্রানীর কাছে পৃথিবীর সব জিনিসের পরিচয় হয় এই আলোর মাধ্যমে৷ সূর্যের আলো না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হত না৷ কিন্তু সূর্যের যে-আলো আমরা খালি চোখে দেখি তার রং তো সাদা অথচ প্রকৃতিতে আমরা বিভিন্ন রং দেখতে পাই– বিভিন্ন প্রাণী ও গাছপালার মধ্যে৷ রামধনু দেখে প্রাচীন মানুষের মনেও নিশ্চয় এই প্রশ্ন জেগেছিলা যে এই সাতটি রং এল কোথা থেকে?!
প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে কল্পনা করা হয়েছে সূর্যদেবের সাতটি ঘোড়ার কথা৷ এরা হল যথাক্রমে গায়ত্রী, ভারতী, উষ্ণিক, জগতি, ত্রিস্তপ, অনুস্তুপ ও পঙ্গতি৷ এই সাতটি ঘোড়া আসলে সাতটি রং-এর প্রতীক৷ সংক্ষেপে এই রং গুলোর নামকরণ দেওয়া হয়েছে ভিবজিয়োর (VIBYGOR)। V= Violet বা বেগুনি। I= Indigo বা গাঢ়নীল, যদিও এখানে B-ও বোঝায় নীল রং-কে৷ ইন্ডিগো রং– বেগুনী ও নীলের মাঝামাঝি৷ তরঙ্গের হিসেবে এদের পার্থক্য বোঝা সহজ হবে– তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অংক থেকে; এই অংকের ব্যাপারটায় পরে আসছি৷ আলোর আলোচনায় এই অংক জানাটা জরুরী৷ বাকি অক্ষর গুলির মধ্যে G = green বা সবুজ, Y= yellow বা হলুদ৷ O= orange বা কমলা আর R = Red বা লাল৷ আমরা খালি চোখে এই সাতটি রং দেখতে পাই৷
কিন্তু সূর্যের আলোর মধ্যে আল্ট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মিও রয়েছে যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনী আলোর চেয়ে কম৷ তবে সূর্যের আলোয় সবচেয়ে বেশী রয়েছে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লালের চেয়ে বেশী৷ আমাদের এবং অন্য প্রাণীর শরীর থেকে ইনফ্রারেড রশ্মি নিয়ত বিকীর্ণিত (radiated) হচ্ছে৷ অতিবেগুনী বা অবলোহিত রশ্মি আমরা দেখতে না পেলেও কিছু প্রাণী আছে যারা এই সব রশ্মি দেখতে পায়৷ এক ধরনের মাকড়সা আছে যারা অতিবেগুনী ও সবুজ আলো দেখতে পায়৷ আবার সাপেরা অবলোহিত রশ্মি দেখতে পায়৷ কিছু কীট পতঙ্গ আছে যাদের চোখে ধরা পড়ে অন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি৷ যেমন মৌমাছি দেখতে পায় অতিবেগুনি, নীল ও হলুদ রং৷ আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না৷ এখন আলোর মৌল ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব৷
উপরের আলোচনায়, ‘আলো’কে একটি তরঙ্গ হিসেবেই ধরেছি৷ তরঙ্গের সঙ্গে আলোর কম্পনাংকের একটা গাণিতিক সম্পর্ক রয়েছে৷ আলোর সম্পর্কে নিউটনের করপাসকুলার থিয়োরী বিজ্ঞানে সুপরিচিত৷ যদিও নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা এটা মেনে নেন নি৷ আর সেসময়ে প্রযুক্তি এত উন্নত ছিলনা যে আলো আসলে অতি ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি– এটা প্রমাণ করা যায়৷ ভারতে নিউটনেরও বহু বহু বছর আগে জৈন দার্শনিকরা আলোকে এই রকম কণার প্যাকেজ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন৷ তবে নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী হাইগেনস (Christiaan Huygens- ১৬২৯-১৬৯৩), যিনি গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও উদ্ভাবক হিসেবে বিজ্ঞান জগতে একটি অতি সুপরিচিত নাম, তিনি আলোর তরঙ্গ-ধর্মের থিয়োরীকেই সমর্থন করেছেন৷ পরবর্তীতে আলোর তরঙ্গ-ধর্মকে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর নাম থমাস ইয়ং (Thomas young – ১৭৭৩-১৮১৯)৷ তাঁর এই পরীক্ষাটি একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা বললে অত্যুক্তি হবেনা৷ এই পরীক্ষাটি ভবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে খ্যাত ৷ বাংলায় বলা যায় জোড়া ছিদ্র পরীক্ষা৷
পরীক্ষাটি অত্যন্ত সহজ৷ একটি পর্দায় দুটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র (একটির নীচে আর একটি থাকবে) করে টাঙ্গিয়ে তার পিছনে একটি স্ক্রিণে রাখা হবে৷ এবার পর্দায় আলো ফেললে ওই দুটি ছিদ্র দিয়ে আলো পড়বে খাড়া ভাবে দাঁড় করানো ওই স্ক্রিণে উপর কিন্তু সব জায়গায় সাদা রং দেখতে পাওয়া যাবে না– দেখা যাবে সাদা কালোর একটা প্যাটার্ণ ৷
একটা ছিদ্র যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় এই প্যাটার্ণটি আর দেখা যাবেনা৷ দেখা যাবে একটি উজ্ব্বল পাড় (fringe) আলোকে তরঙ্গ ধরলে অংক কষে এটি ব্যাখ্যা করা যায়৷ পরবর্তী কালে যখন কোয়ান্টাম থিয়োরী আবিষ্কার হয় তখন এই ধরণের জোড়া ছিদ্র পরীক্ষায় অদ্ভুত সব জিনিস লক্ষ্য করা যায় ৷
আমাদের বিষয় বস্তু যেহেতু আলো, আমরা সে ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনায় যাব না৷ আমরা চলে আসব বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে৷
১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (Max Planck- ১৮৫৮-১৯৪৭) কালো-বস্তুর বিকিরণের (black body radiation) উপর গবেষণা করে জানালেন, আলোকে অনেক কণার সমষ্টি হিসেবে না ধরলে, পরীক্ষায় যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা কোন থিয়োরীতেই মিলছে না৷ প্ল্যাঙ্ক নিজে যে ফরমুলা আবিষ্কার করেন তা এখন প্ল্যাঙ্ক বিভাজন (Planck Distribution ) হিসেবে পরিচিত৷
আলো যে-কণার সমষ্টি তার নাম হল ‘ফোটন’৷ অবশ্য এই নামকরণ প্রথমে করেন (১৯২৬ সালে) জি এস লুইস (G.S.Lewis -১৮৭৫-১৯৪৬)৷ এর আগেই আইনস্টাইন (Albert Einstein- ১৮৭৯-১৯৫৫) আলোর কোয়ান্টাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্টের থিয়োরীর মাধ্যমে৷ বস্তুত আইনস্টাইন পদার্থ বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পান তাঁর এই কাজের জন্য৷ আইনস্টাইনের আর একটি আবিষ্কার হল বিশেষ আপেক্ষিকতা বাদ৷ আপেক্ষিক গতির গ্যালিলোওর (Galileo Galilei -১৫৬৪- ১৬৪২) ধারণার সঙ্গে এর প্রধান তফাৎ হল আলোর গতি ভ্যাকুয়ামে একটি ধ্রুবক এবং আলোর গতির থেকে বেশী গতি সম্পন্ন আর কোনো কণা বা বস্তু হতে পারে না৷ আগের গ্যালিলিয়ান থিয়োরীর সঙ্গে মূল তফাৎ এটিই৷ এ ছাড়া আলোর কোয়ান্টাম ধর্ম নিয়ে সহজ করে বলতে গেলে – একটি ফোটন কণার একটি নির্দিষ্ট শক্তি আছে৷ এই শক্তি তার কম্পনাংকের উপর নির্ভর করে৷ এবং যে শক্তি কোনো বস্তুর থেকে বিকিরিত হয় তা যথেচ্ছ ভাবে হবেনা৷ যদি আমরা শক্তির কোনো একক ধরি তবে শক্তি এক একক, দুই একক বা তিন একক ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্য দিয়ে নির্ণীত হবে৷
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোস প্ল্যাঙ্ক বিভাজনে একটি সংখ্যাতাত্বিক ব্যাখ্যা দেন এবং আইনস্টাইন স্বয়ং বোসের পেপারটা ছাপার ব্যবস্থা করেন এবং বলেন এই আবিষ্কারের ফল সুদূর প্রসারী৷ এখন এই পরিসংখ্যানটি বোস-আইনস্টাইন বিভাজন বা অনেক সময় শুধু বোস-বিভাজন হিসেবে খ্যাত৷ যে সব কণা বোস-বিভাজন মেনে চলে তারা বোসন হিসেবে পরিচিত৷ বোসের সম্মানার্থে পল ডিরাক (Paul Dirac- ১৯০২-১৯৮৪) যিনি আধুনিক কোয়ান্টাম তত্বের অন্যতম দিকপাল, তিনি এই নাম করণ করেন৷ অন্য কণারা ফার্মিয়ন হিসেবে পরিচিতা৷ এই নাম করণটিও করেন ডিরাক৷ এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আলো তাহলে কী? কণা না তরঙ্গ৷ দুটিই সত্য৷ ডঃ জেকিল ও মিঃ হাইডের মত আলোর দ্বৈত চরিত্র আছে৷ ফরাসী বিজ্ঞানী লুই দ্য ব্রইলির (Louis de Broglie- ১৮৯২-১৯৮৭) থিয়োরী অনুযায়ী এই ধর্ম শুধু ফোটন কণা নয় সমস্ত কনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য৷ পরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন ইলেকট্রন ও নিউট্রনের ক্ষেত্রে দ্য ব্রইলির থিয়োরী সত্য৷
আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?
যে সাতটি রং আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তার মধ্যে বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৩৮০ ন্যানোমিটার, আর লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানো মিটার৷ এক ন্যানো মিটার হল এক মিটারের একশ কোটি ভাগের এক ভাগ৷ এর থেকে বোঝা যায় আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত ছোট হতে পারে৷ আবার মাইক্রো ওয়েভ বা অণু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক মিলি মিটার থেকে এক মিটার হতে পারে৷ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোস (J.C.Bose -১৮৫৮-১৯৩৭) এই মাইক্রো ওয়েভ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন৷ তাঁকেই রেডিও আবিষ্কারক হিসেবে এখন ধরা হয়৷ যদিও এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার তিনি পান নি, পেয়েছিলেন মার্কনী (Guglielmo Marconi- ১৮৭৪-১৯৩)৷ ভারতীয় বিজ্ঞানী সি ভি রমন (C.V Raman – ১৮৮৮-১৯৭০) আলোর সঙ্গে ম্যাটারের সংঘর্ষ নিয়ে কাজ করেছিলেন৷ ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান তাঁর এই গবেষণার কাজ এখন ‘রমন এফেক্ট’ হিসেবে বিজ্ঞান জগতে সুপরিচিত৷
এখানে বলে রাখা উচিৎ আলোর এই দ্বৈত চরিত্র খুব বড় বস্তুর ক্ষেত্রেও খাটবে৷ তবে খুব বেশী তরঙ্গ দৈর্ঘের জন্য বড় বস্তুর তরঙ্গ-ধর্ম পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা সহজ হবে না৷
এবার আলোর আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম বা বিশেষত্ব বলব যা আবিষ্কারের ফলে আমরা ল্যাপটপ, কমপিউটার, সেল-ফোন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারছি। ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell- ১৮৩১-১৮৭৮) ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী৷ তিনি অমর হয়ে থাকবেন চারটি ইকুয়েশনের জন্য যা এখন ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন হিসেবে খ্যাত৷ এই ইকুয়েশনগুলি থেকে প্রমাণ হয় আলো একটি বিদ্যুত-চৌম্বকিয় তরঙ্গ (Electromagnetic wave)। শুধু তাই নয়, এই ইকুয়েশনগুলি থেকে শুধু অংক কষে আলোর গতিবেগ বার করা যায় যা পরীক্ষায় প্রাপ্ত সংখ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়৷ শূন্যে এই গতি বেগ হল প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে৷ এটি একটি ধ্রুবক৷ আইনস্টাইনের এই আবিষ্কারের ফলে (যা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বা স্পেশাল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি হিসেবে পরিচিত) আমরা জানি absolute time বলে কিছু নেই) অবশ্য ম্যাক্স ওয়েলের এই আবিষ্কারের পিছনে অবদান ছিল যাঁদের নাম তাঁদের আমরা প্রায় রোজই স্মরণ করি, কিন্তু অনেকে ই পিছনের ইতিহাস জানিনা ৷যেমন ফ্যারাডে (Michael Farade , ১৭৯১-১৮৬৭), Ampere (Andre Ampere- ১৭৭৫-১৮৩৬; কারেন্টের ইউনিট এনার নামে করা হয়েছে ) ওম ( Georg Simon Ohm -১৭৮৯-১৮৫৪)।
আমরা যে সমস্ত ইলেকট্টিক গ্যাজেট ব্যাবহার করি তার রেসিস্টান্সের একক হল ওম ৷
পাখার রেগুলেটরে যে ক্যাপাসিটান্স থাকে তার একক হল ফ্যারাডে ৷
ফ্যারাডের আবিষ্কারের ফলে আমরা পেয়েছি পাখা ও জেনারেটর ৷
আলোর ইতিহাস তাই একই সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাস৷ বহু শতকের বহু বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা জানতে পেরেছি আলোর ধর্ম৷ আমরা জেনেছি আমাদের খালি চোখে যে রং ধরা পড়ে সেটা আলো। আবার এক্স-রে ও গামা-রের মত শক্তিশালী রষ্মি (যা ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়) সেগুলিও আলোর আর এক রূপ৷ আর একটি কথা বলি যা স্কুলেরা ছেলেরাও জানে৷ আমাদের চোখে কোনো জিনিস সবুজ বা কোনো জিনিস লাল প্রতীয়মান হয় কী করে? সবুজ রংএর বস্তু অন্য সব রং শুষে নেয় সবুজ রং ছাড়া– শুধু সবুজ রং প্রতিফলিত করে৷ তাই বস্তুটিকে সবুজ দেখায়৷ যদি কোন বস্তু সমস্ত রং-ই শুষে নেয় তবে আমরা তাকে কালো দেখি৷ আর সমস্ত রং যে বস্তু ফিরিয়ে দেয়– প্রতিফলিত করে, তা আমাদের কাছে সাদা রং হিসেবে প্রতীয়মান ৷হয় ৷
যেহেতু আলোর গতি একটি ধ্রুবক এবং তা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পনাংকের গুণ ফল, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেশী হলে কম্পনাংক কম হবে আবার দৈর্ঘ্য কম হলে কম্পনাংক বেশী হবে ৷আলোর শক্তি তার কম্পনাংকের সমানুপাতিক৷ একটি ফোটনের শক্তি হল তার কম্পনাংকের সঙ্গে একটি ধ্রুবকের গুণ ফল৷ এই ধ্রুবকটিকে h ধরা হয়। এর আর একটা নাম প্ল্যাঙ্ক কনস্টান্ট৷ এটি কোন অংকে দেখলেই আমরা বুঝব এটি কোয়ান্টাম মেকানিকসের অংক৷ গত বছর তিন বিজ্ঞানী পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান আলোর সাহায্যে পরমাণুর ভিতর ইলেকট্রনের গতিবিধি নিরীক্ষণের জন্য৷ এঁরা হলেন যথা ক্রমে পিয়ের অগস্তিনি, (Pierre Agostini), অ্যান লুলিয়ের (Anne L’ Huillier ) ও ফেরেন্স ক্রাউস (Ferenc Krausz)৷
এঁরা অতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য আলোর পালস তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন৷ তাঁদের কাজকে অ্যাটোসেকেন্ড ফিজিক্স (Attosecond Physics ) বলা হয়৷ এক Attosecond কত ক্ষুদ্র সময় আমরা কল্পনা করতে পারব না৷ এক সেকেন্ডকে যদি একশ কোটি ভাগ করি এবং এই ভাগের আবার একশ কোটি ভাগ করি তা হলে পাব এক Attosecond৷ কিন্তু আলোর মধ্যে আরও কী রহস্য লুকিয়ে আছে এখন তা বলা যাবেনা৷ বিজ্ঞানের কাজই হল জানার মাঝে অজানার সন্ধান ৷